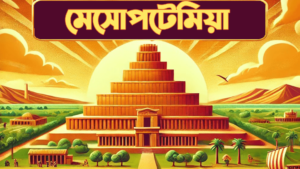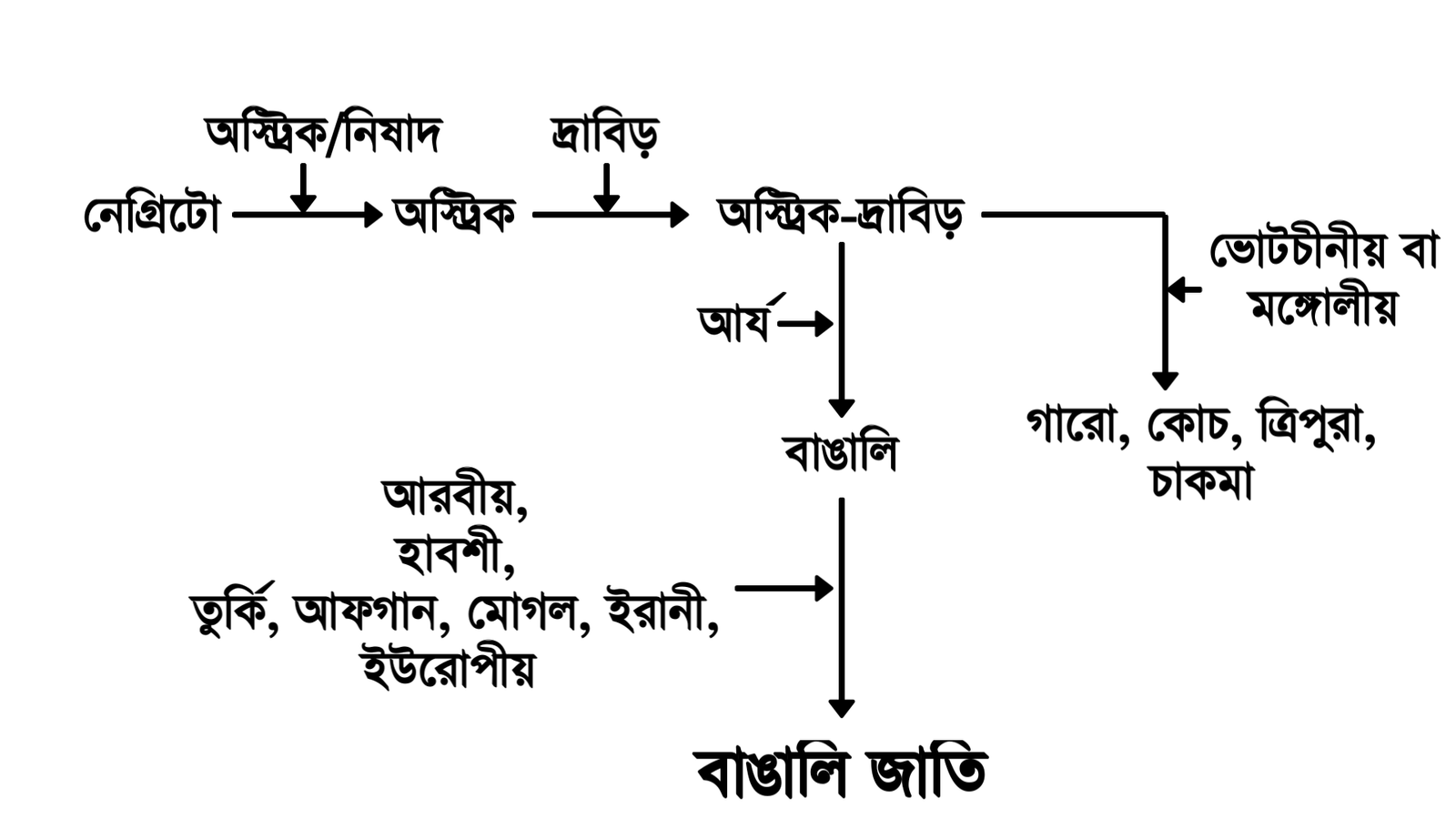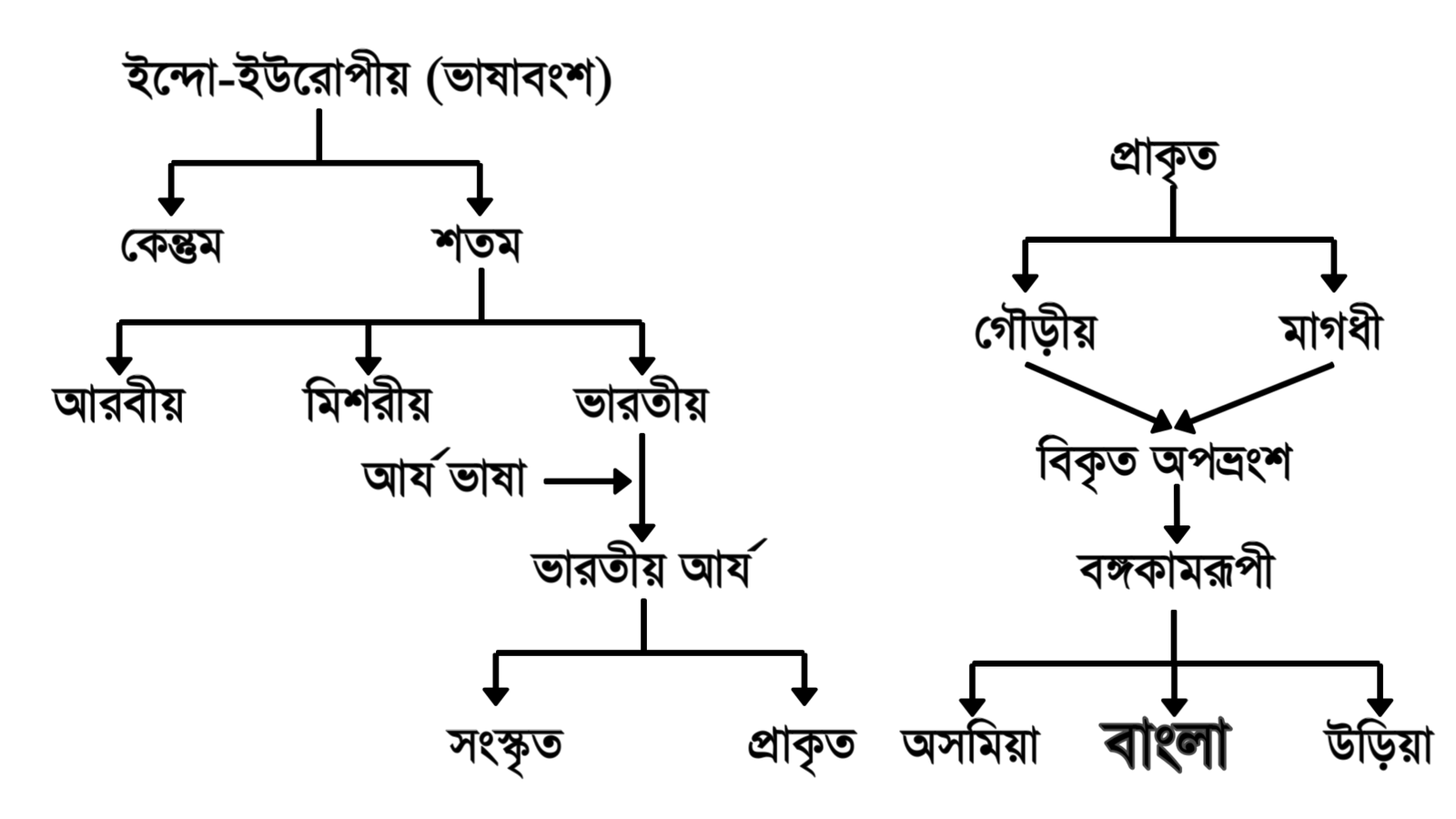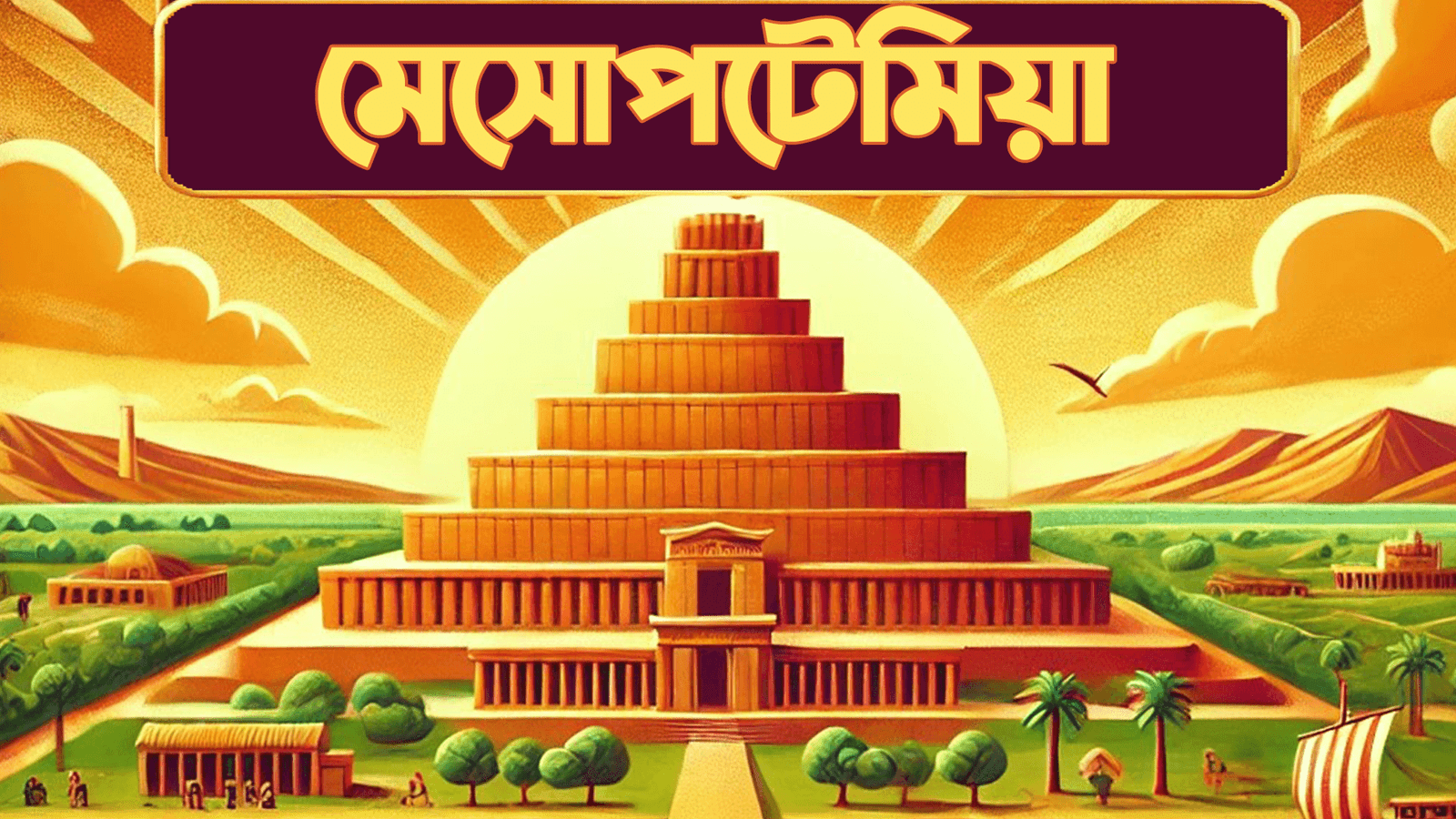বাংলা বলতে আমরা যে অঞ্চলটিকে বুঝি বহুকাল পূর্বে তা এমন ছিল না। বাংলার বিভিন্ন অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত ছিল; যা জনপদ নামে পরিচিত। চতুর্থ শতকে মৌর্য শাসনামল, মৌর্য হতে গুপ্ত যুগ, গুপ্ত পরবর্তী যুগ, পাল শাসনামল, সেন শাসনামল প্রভৃতি সময়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি ও সাহিত্য গ্রন্থে প্রাচীন বাংলায় এরুপ ১৬টি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলো হলো:
- পুন্ড্র
- হরিকেল
- বঙ্গ
- গৌড়
- সমতট
- বরেন্দ্র
- রাঢ়
- চন্দ্রদ্বীপ
- সপ্তগাঁও
- কামরুপ
- তাম্রলিপ্ত
- আরাকান বা রূহ্ম
- সুহ্ম
- বিক্রমপুর
- বাকেরগঞ্জ ইত্যাদি।
বিভিন্ন সময় এসব জনপদের সীমা ও বিস্তৃতি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এদের মধ্যে প্রধানত ৫টি জনপদ থেকে বর্তমান বাংলাদেশের জন্ম হয়। এগুলো হল পুন্ড্র, বঙ্গ, হরিকেল, সমতট এবং গৌড়। এছাড়া অপ্রধান জনপদসমূহের মধ্যে রয়েছে বরেন্দ্র, রাঢ়, চন্দ্রদ্বীপ ইত্যাদি।
নিচে প্রধান জনপদসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।
পুন্ড্র
বাংলাদেশের জনপদসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম জনপদ হল পুন্ড্র বা পৌন্ড্র। পুন্ড্রদের আবাসস্থলই পুন্ড্র বা পুন্ড্রবর্ধন নামে পরিচিত। বৃহত্তর বগুড়া (বর্তমান নাম মহাস্থানগড় যা বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় অবস্তিত), রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ নিয়ে এ জনপদ গঠিত হয়েছিল। এ রাজ্যের রাজধানী ছিল পুণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রনগর। পুন্ড্রবর্ধনভুক্তির একটি নগর ছিল কোটিবর্ষ। বৈদিক সাহিত্য ও মহাভারতেও প্রাচীন পুণ্ড রাজ্যের উল্লেখ আছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বানগড় গ্রামে এই নগরের ধ্বংশাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। ‘পৌন্দ্রিক’ শব্দ থেকে ‘পুন্ড্র’ নামের উৎপত্তি। এর অর্থ- আখ বা চিনি। পুন্ড্র আখের একটি প্রজাতি। আখের অত্যাধিক ফলনের জন্যই এ অঞ্চল পুন্ড্রভূমি নামে পরিচিত ছিল।
আনুমানিক খ্রি. পূ. চার শতকে এই নগর গড়ে উঠেছিল। ১৮০৮ সালে ফ্রান্সিস বুকানন হেমিল্টন সর্বপ্রথম স্থানটি আবিষ্কার করেন। ১৮৭৯ সালে আলেকজান্ডার কানিংহাম স্থানটিকে প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধনের ধ্বংশাবশেষ হিসাবে শনাক্ত করেন।
কথিত আছে এ অঞ্চলে পরশুরামের সাথে ফকির বেশী হযরত শাহ সুলতান মাহমুদ বলখীর যুদ্ধ (১২০৫-১২২০ খ্রি.) হয়। যুদ্ধে পরশুরাম পরাজিত ও নিহত হয়। ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়। শাহ-সুলতান বলখির মাজার রয়েছে এ অঞ্চলে।
সম্রাট অশোক নির্মিত বৌদ্ধ স্তম্ভ যা বেহুলা-লখিন্দরের বাসর ঘর নামে পরিচিত ইত্যাদি এ অঞ্চলের দর্শনীয় স্থান।
মহাস্থানগড়ে একটি ব্রাহ্মী লিপি পাওয়া গেছে। এটি হচ্ছে বাংলার প্রাচীনতম শিলালিপি।
এছাড়াও দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে রয়েছে পরশুরামের প্রাসাদ, খোদার পাথর ভিটা, বৈরাগীর ভিটা, গোবিন্দের ভিটা, লক্ষীন্দরের মেদ, গড়ের পূর্ব পাশে করতোয়া নদীর তীরে শীলাদেবীর ঘাট ইত্যাদি।
উল্লেখ্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে প্রাচীন পুন্ড্র রাজ্যের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। পুন্ড্রনগর মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল।
২০১৭ সালে মহাস্থানগড়কে সার্ক সাংস্কৃতিক রাজধানী ঘোষণা করা হয়।
বঙ্গ
বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বাকলা (বরিশাল), বিক্রমপুর, পটুয়াখালি, (বাখেরগঞ্জ)। পাঠান আমলে সমগ্র বাংলা বঙ্গ নামে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।
গঙ্গার দুই প্রধান স্রোতোধারা ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী ত্রিভুজাকৃতির ভূখন্ড। বঙ্গ থেকেই বাঙালি জাতির উৎপত্তি। প্রাচীন গ্রিক ও ল্যাটিন ক্লাসিক লেখকগণের বর্ণনা অনুসারে খ্রি. পূ. ৩২৬ অব্দের দিকে গঙ্গারিডাই নামক পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল এখানে। এখানেই প্রাচীনতম ব্রাহ্মী লিপি পাওয়া যায়।
প্রাচীন বঙ্গ ছিল একটি শক্তিশালী রাজ্য। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে বঙ্গ নামে উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া রামায়ণ, মহাভারত এবং কালিদাসের রঘুবংশ গ্রন্থে বঙ্গ নামের উল্লেখ আছে।
হরিকেল
সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা। চীনা ভ্রমণকারী ইৎ সিং এর মতে, হরিকেল ছিল পূর্ব ভারতের শেষ সীমায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত দুইটি শিলালিপিতে হরিকেলকে সিলেটের সমর্থক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
সমতট
চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর বিবরণ অনুযায়ী সমতট বঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ পূর্বাংশের একটি নতুন রাজ্য। মেঘনা নদীর মোহনাসহ বর্তমান কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল সমতটের অন্তর্ভুক্ত। রাজধানী কুমিল্লার ১২ মাইল পশ্চিমে বড় কামতা। ময়নামতিতে অবস্তিত শালবন বিহার এ জনপদের প্রাচীনতম নিদর্শন।
গৌড়
মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা নিয়ে গঠিত। প্রাচীন বাংলার জনপদগুলাকে শশাঙ্ক গৌড় নামে একত্রিত করেন। রাজধানী মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণ। পাণিনির গ্রন্থে সর্বপ্রথম গৌড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থেও এ জনপদের শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। হর্ষবর্ধনের শিলালিপি হতে প্রমাণিত হয় যে, সমুদ্র উপকূল হতে গৌড় দেশ খুব বেশি দূরে ছিল না।
অপ্রধান জনপদসমূহ
বরেন্দ্র
উত্তরবঙ্গের একটি জনপদ। বগুড়া,পাবনা, রাজশাহী বিভাগের উত্তর পশ্চিমাংশ, রংপুর ও দিনাজপুরের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল। পাল রাজারা উত্তরবঙ্গকে তাদের পিতৃভূমি মনে করত। সেজন্য এর নামকরণ করেছিল বারিন্দ্রী। এই বারিন্দ্রী থেকে বরেন্দ্র শব্দের উৎপত্তি। বর্তমান করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরের লালমাটি সমৃদ্ধ অঞ্চলই বরেন্দ্রভূমি নামে পরিচিত। গঙ্গা ও করতোয়া নদীর পশ্চিমাংশের মধ্যবর্তী অংশকে রামায়ণে বারিন্দ্রীমণ্ডল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
রাঢ়
পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাংশ (বর্ধমান জেলা)। অজয় নদী রাঢ় অঞ্চলকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। উত্তর রাঢ় বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ সমগ্র বীরভূম জেলা এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা নিয়ে গঠিত। আর দক্ষিণ রাঢ় বর্ধমানে দক্ষিণাংশ হুগলি বহুলাংশ এবং হাওড়া জেলা। উল্লেখ্য এই রাঢ় অঞ্চল তথা কলকাতার ভাষাকেই বাংলা ভাষার প্রমিতরূপ বলে গণ্য করা হয়।
চন্দ্রদ্বীপ/ বাকলা
বালেশ্বর ও মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্তিত। মূলত বরিশাল; তাছাড়া আছে পিরোজপুর, পটুয়াখালি, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, বিক্রমপুর, মুন্সিগঞ্জ। আইন ই আকবরী গ্রন্থে বাকলা পরগনা নামে উল্লেখ করা হয়েছে। পাল যুগে এটি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের শাসনাধীন ভূখণ্ডরূপে শাসিত হতো।
তাম্রলিপ্ত
হরিকেলে ও রাঢ়ের দক্ষিণে অবস্থিত মেদিনীপুর জেলা ছিল এর প্রাণকেন্দ্র। গ্রিক পন্ডিত টলেমির মানচিত্রে তমলিটিস নামের যে বন্দর নগরীর উল্লেখ করা হয়েছিল তাই তাম্রলিপ্ত। পেরিপ্লাস নামক গ্রন্থে এবং টলেমি, ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং ও ইৎ সিংয়ের বিবরণেও এই তাম্রলিপ্ত জনপদের নাম বন্দর হিসেবে উল্লেখ আছে। সপ্তম শতক হতে এটা দণ্ডভুক্তি নামে পরিচিত হতে থাকে। আট শতকের পর হতেই তাম্রলিপ্ত বন্দরের সমৃদ্ধি নষ্ট হয়ে।
সপ্তগাঁও
খুলনা ও সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল।
কামরূপ
জলপাইগুড়ি, আসামের বৃহত্তর গোয়ালপাড়া জেলা,বৃহত্তর কামরূপ জেলা।
রূহ্ম বা আরাকান
কক্সবাজার, মায়ানমারের কিছু অংশ, কর্ণফুলি নদীর দক্ষিণ অঞ্চল।
সুহ্ম
গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের দক্ষিণ ভূভাগ। আধুনিক মতে বর্ধমানের দক্ষিণাংশ, হুগলির বৃহদাংশ, হাওড়া এবং বীরভূম জেলা।
বিক্রমপুর
মুন্সিগঞ্জ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল।
বাকেরগঞ্জ
বরিশাল, খুলনা, বাগেরহাট।